যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে টাকা লাগে। সেটা জোগাড় করতে প্রার্থীরা বেশ কিছু বিকল্প বেছে নেন। প্রার্থীরা তাদের নিজস্ব অর্থ দিয়ে প্রচারণা চালাতে পারেন, অথবা ব্যক্তিগত দাতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। তহবিলের আরেকটি উৎস রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটি গ্রুপ থেকে আসে, যা প্যাক (পিএসি) বা সুপারপ্যাক নামে বেশি পরিচিত।
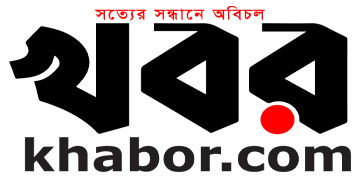
মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থীদের খরচ কত, কিভাবে অর্থ আসে
খবর প্রকাশিত: ৩০ অক্টোবর, ২০২৪, ১২:৩২ পিএম

সরকারি তহবিল থেকেও অর্থ পেতে পারেন প্রার্থীরা। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যয়ের হিসাবের কঠোর সীমাবদ্ধতা মেনে চলতে হয়। ফলে গত কয়েকটি নির্বাচনে মূলধারার প্রার্থীরা এই বিকল্পটি বরাবরই এড়িয়ে গেছেন।
কমলা হ্যারিস কত টাকা জোগাড় করেছেন?
মার্কিন নির্বাচনে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করে ওয়াশিংটনভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ওপেনসিক্রেটস।
এর বাইরে বাইরের কিছু গ্রুপ কমলাকে সমর্থন করে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৫৯ মিলিয়ন ডলারের (চার হাজার কোটি টাকা) বেশি অর্থ দিয়েছে।
মোট সংগ্রহের ৫৬ শতাংশই এসেছে বড় বড় দান থেকে। বাকি ৪৪ শতাংশ সংগ্রহ হয়েছে ২০০ ডলারের নিচে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ছোট ছোট অবদানের মাধ্যমে।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংগ্রহ কত?
অন্যদিকে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প কমলা হ্যারিসের চেয়ে অনেক কম অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তার আনুষ্ঠানিক প্রচারণা দল ৩৬৭ মিলিয়ন ডলার (প্রায় চার হাজার ৩০০ কোটি টাকা) সংগ্রহ করেছে।
ওপেনসিক্রেটসের তথ্য অনুসারে, বাইরের গ্রুপগুলো আরো ৫৭২ মিলিয়ন ডলার (ছয় হাজার ৮০০ কোটি টাকা) ট্রাম্পের তহবিলে যোগ করেছে। এর ফলে ট্রাম্পের মোট তহবিল দাঁড়িয়েছে ৯৪০ মিলিয়ন ডলারে (১১ হাজার ১০০ কোটি টাকা)।
ট্রাম্পের তহবিলের ৬৮ শতাংশেরও বেশি অবদানের এসেছে অতিধনীদের সমর্থন থেকে।
তহবিল কি নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করে?
গত দুই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের চেয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তহবিল বড় ছিল। তার পরও ২০২০ সালে বাইডেনের কাছে হারার আগে ২০১৬ সালে হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে জিতেছিলেন ট্রাম্প।
পেনসিলভানিয়ার পেন স্টেট হ্যারিসবার্গের জননীতি ও প্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড্যান ম্যালিনসন মনে করেন, এই অসংগতিই প্রমাণ করে, অর্থ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটাই নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করতে পারে না। তবে ‘বিলিয়ন ডলারের বিষয়ে’ পরিণত হওয়া অনুদানকে গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করতে হবে বলেও মনে করেন তিনি।
তিনি বলেন, ‘প্রার্থী, দল, রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটি ও অন্য সংস্থাগুলোকেও প্রচার চালানোর জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে হয়।’
শুধু সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টই নন, মার্কিন সিনেটের ১০০টি আসনের মধ্যে ৩৪টিতে এ বছর নির্বাচন হবে। হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে ৪৩৫টি আসনে নির্বাচন হবে।
ওপেনসিক্রেটসের তথ্য অনুযায়ী, এসব আসনে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সিনেট প্রার্থীদের সংগৃহীত মোট তহবিল দাঁড়িয়েছে ১.৩৮ বিলিয়নে (১৬ হাজার কোটি টাকা)। সমষ্টিগতভাবে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রার্থীরা ১.৭৮ বিলিয়ন ডলার (২১ হাজার কোটি টাকা) সংগ্রহ করেছেন।
কে দান করতে পারে?
প্রার্থীদের তহবিলে কারা দান করতে পারবেন, কারা পারবেন না, এ নিয়ে ফেডারেল নির্বাচন কমিশনের কঠোর নিয়ম রয়েছে।
শুধু মার্কিন নাগরিক বা গ্রিনকার্ডধারীরাই পার্টি বা প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর তহবিলে দান করতে পারেন। এর ফলে বিদেশি নাগরিকরা কোনোভাবেই নির্বাচনী তহবিলে দান করতে পারবেন না। দানের সীমাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।
সরকারি ঠিকাদার, করপোরেশন, জাতীয় ব্যাংক, শ্রমিক ইউনিয়ন ও অলাভজনক সংস্থাগুলোও ফেডারেল নির্বাচনে প্রার্থী বা দলগুলোর তহবিলে সরাসরি অবদান রাখতে পারবে না।
প্যাক ও সুপারপ্যাক কী?
পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (পিএসি) দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন নির্বাচন ব্যবস্থার একটি অংশ। এই লবিং গ্রুপগুলো প্রার্থীদের পক্ষে অর্থ ও ভোট সংগ্রহে কাজ করে। তাদের অনুদান সীমিত এবং দাতাদের তালিকা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক।
কিন্তু ২০১০ সালের প্রচারাভিযানে অর্থায়নের নিয়মকানুনে ব্যাপক পরিবর্তিত আসে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সে বছর বাকস্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে করপোরেশন ও ইউনিয়নগুলোর ক্ষেত্রে প্রচারণায় অর্থ প্রদানের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। এই সিদ্ধান্তের পর করপোরেশন ও ইউনিয়নগুলো সমন্বিতভাবে বেশ কয়েকটি সুপারপ্যাকের জন্ম দিয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলো ব্যক্তি, ইউনিয়ন বা করপোরেশন থেকে সীমাহীন অর্থ সংগ্রহ করতে পারে এবং অনুদান দেওয়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশেরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।
প্যাক ও সুপারপ্যাকগুলো সরাসরি কোনো প্রার্থীকে অনুদান দিতে পারে না এবং তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে হয়। তবে কিছু নিয়মকানুন এ ক্ষেত্রেও শিথিল করা হয়েছে।
প্রচারাভিযানে বড় অবদানের সমস্যা
প্রচারাভিযানে এই দানব্যবস্থা অনেক ভোটারের মনে এমন ধারণা তৈরি করে যে অর্থদানের ফলে রাজনীতিবিদদের কাছে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে দুর্নীতি বা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা নষ্ট হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে।
মেলিন্ডা ফ্রেঞ্চ গেটস ও জর্জ সোরোসের মতো ধনী আমেরিকানরা কমলা হ্যারিসকে সমর্থনকারী গ্রুপগুলোতে লাখ লাখ ডলার দান করেছেন। কেউ কেউ নিজস্ব সুপারপ্যাক প্রতিষ্ঠা করেছেন।
ফিন্যানশিয়াল টাইমসের তথ্য অনুসারে, বিলিয়নেয়ারদের আরেকটি গ্রুপ ট্রাম্পপন্থী সুপারপ্যাকগুলোতে সম্মিলিতভাবে ৩৯৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা) অনুদান দিয়েছেন। এই গ্রুপে রয়েছেন ইলন মাস্ক, টিমোথি মেলন, মিরিয়াম অ্যাডেলসন ও রিচার্ড উইহেলিনের মতো অতিধনীরা।
এই বিশাল অর্থ অনুদান দেওয়ার মানে, ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা কি না, সেটি একটি জটিল প্রশ্ন। ড্যান ম্যালিনসন মনে করেন, ‘অর্থ দেওয়া মানে ভোট ও নীতি কিনে নেওয়া—এটা বলাটা সহজ নয়।’
ম্যালিনসন বলেন, এই অর্থ দানের ফলে দাতাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার সময় তাদের চাহিদা জানানোর রাজনৈতিক সুযোগ তৈরি হয়। তিনি অবশ্য মনে করেন, ‘তবে এর মানে এই নয় যে দাতারা যা চাইবেন সবই পেয়ে যাবেন।’
প্রচারাভিযান কোথায় অর্থ ব্যয় করে?
কোটি কোটি ডলার খরচ হাতে থাকায় সেটা কিভাবে ও কোন খাতে ব্যয় করা হবে, সে ব্যাপারে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় প্রার্থীর প্রচারদল ও প্রেশার গ্রুপকে। নির্বাচন যেহেতু খুব কাছাকাছি চলে এসেছে এবং বিজয়ের অনেকটাই নির্ভর করবে সুইং স্টেটগুলোর মুষ্টিমেয় ভোটের ওপর। ফলে এখন প্রচার দলগুলো সেখানেই তাদের বেশির ভাগ অর্থ ব্যয় করছে।
এই অঙ্গরাজ্যগুলো রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনে প্লাবিত হচ্ছে। নিজেদের প্রার্থীর পক্ষে ভোট টানতে প্রচারকারীরা ভোটারদের ফোন দিচ্ছেন, কোথাও কোথাও ভোট দিতে রাজি করাতে প্রচারদলের সদস্যরা সরাসরি ভোটারদের বাসায় গিয়ে হাজির হচ্ছেন।
২০২০ সালের নির্বাচন থেকে নির্বাচনী ব্যয়ের ব্যাপারে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ওপেনসিক্রেটসের দেওয়া তথ্য অনুসারে, চার বছর আগে প্রায় ৫৬ শতাংশ ব্যয় ছিল গণমাধ্যমে, ১০ শতাংশ তহবিল সংগ্রহে এবং প্রায় ১৭ শতাংশ প্রচারে ও প্রচারদলের বেতনে। বাকি অর্থের ছয় শতাংশ প্রশাসনে, ৪ শতাংশ কৌশল নির্ধারণ ও গবেষণায় ব্যয় হয়েছিল। অবশিষ্ট ব্যয়কে অশ্রেণিবিন্যাসযোগ্য’ হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের প্রচারাভিযানের ব্যয়ও একই ধরন অনুসরণ করবে।